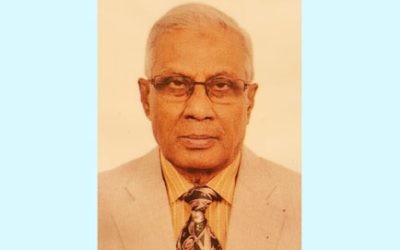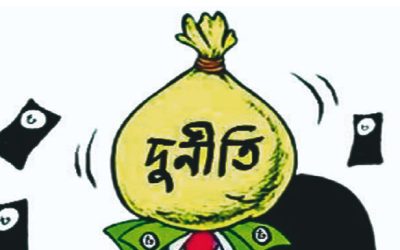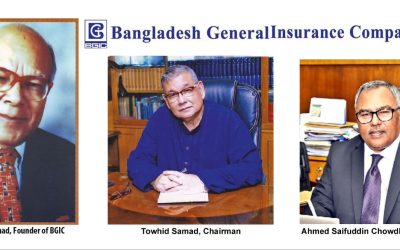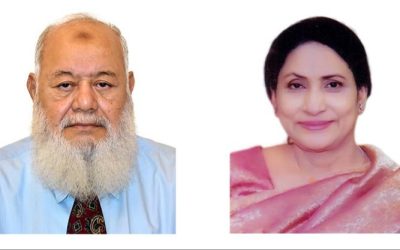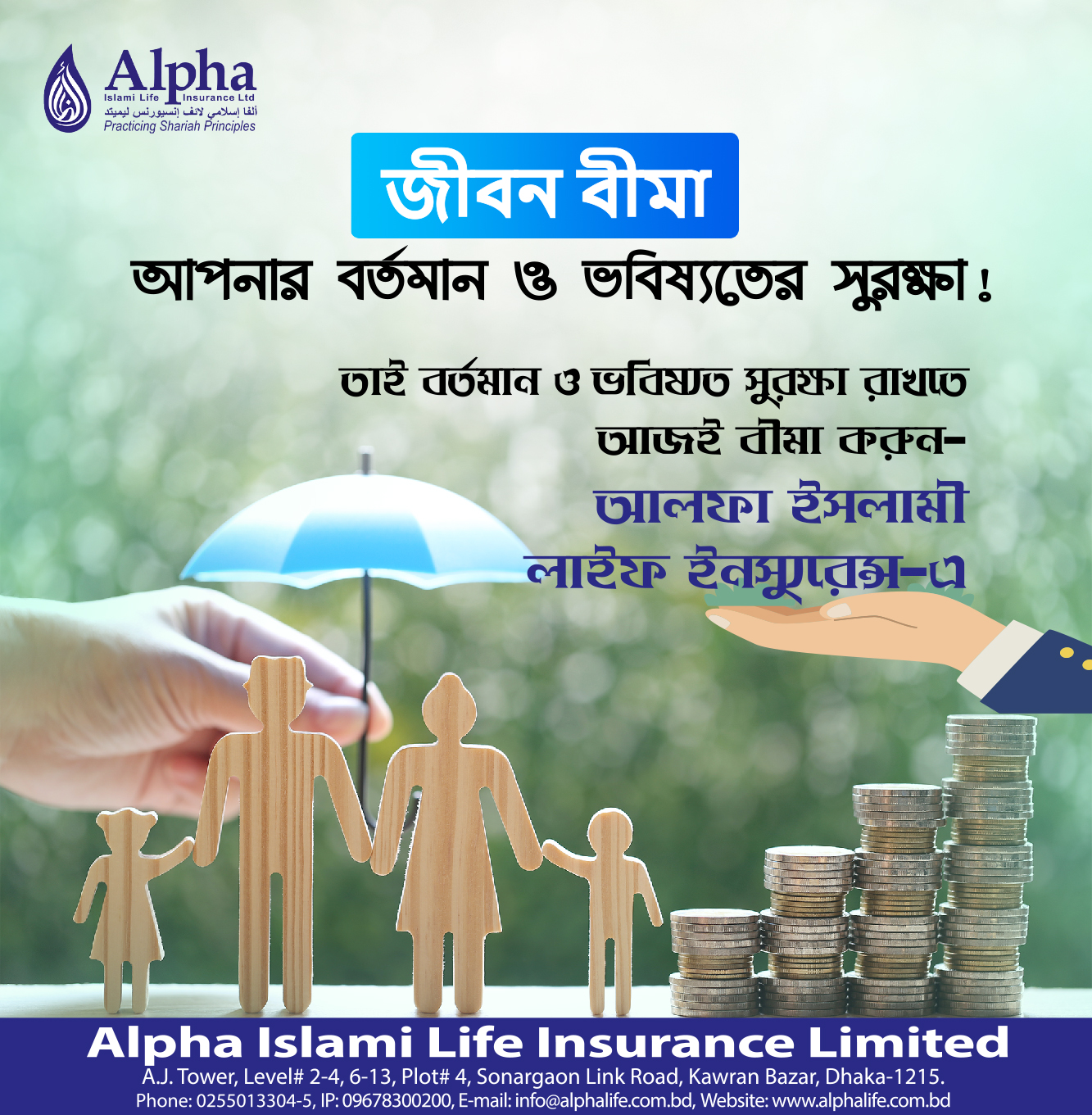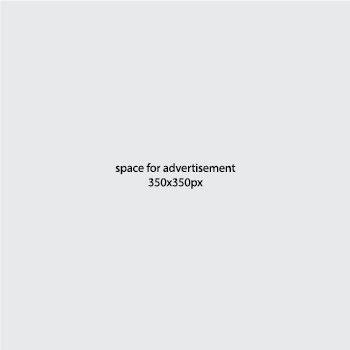অর্থনীতিবিদগণ বিভিন্ন সময় যে সব থিউরি নিয়ে আলোচনা করেন তার সবগুলোই বাস্তবসম্মত বা সব যুগে একই ভাবে কার্যকর তা নিশ্চিত করে বলা যাবে না। অর্থনীতির এমন কিছু থিউরি আছে যা সমাজের বাস্তব চিত্রের প্রতিফলক নয়, বরং মাঝে মাঝে এগুলো সমাজে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে থাকে। মানুষের আচরিত জীবন ধারাকে কেন্দ্র করেই অর্থনীতির বিভিন্ন থিউরি প্রণীত হয়। সময়ের প্রেক্ষিতে এসব থিউরি অনেক সময় অকার্যকর হয়ে পড়ে। কোনোটি বা বিকৃত হয়ে যায়। কিন্তু সাধারণ মানুষকে এসব থিউরি এমনভাবে বলা হয় যেনো তা স্বত:সিদ্ধ এবং সব সময়ই বাস্তবসম্মত। আমরা জাতি হিসেবে অপরিবর্তনীয় ঐতিহ্যের ধারক। নতুন কোনো কিছুই সহজে গ্রহণ করতে চাই না। বা গ্রহণ করার মতো মানসিকতাও আমরা ধারন করি না। ফলে অনেক সময় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। সমাজে প্রচলিত কিছু অর্থনৈতিক থিউরি নিয়ে আলোচনা করলেই বক্তব্যের বাস্তবতা উপলব্ধি করা যাবে।
সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাফল্য প্রদর্শনের জন্য গ্রস ডমেস্টিক প্রোডাক্ট (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি কত হয়েছে তা প্রকাশ করে থাকে। জিডিপি প্রবৃদ্ধি হচ্ছে একটি বছরের তুলনায় পরবর্তী বছর মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদ কতটা বেড়েছে বা কমেছে তার পরিসংখ্যান। যেমন ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে যদি মোট জিডিপি’র পরিমাণ ছিল ১০০ কোটি টাকা। পরবর্তী বছর অর্থাৎ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মোট জিডিপি’র পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ১০৫ কোটি টাকা হয় তাহলে এক বছরের ব্যবধানে অর্থাৎ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের তুলনায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে ৫শতাংশ। কিন্তু জিডিপি প্রবৃদ্ধি গণনা করার সময় দেশের সব উৎপাদন সেক্টরকে বিবেচনায় নেয়া হয় না। ফলে প্রদর্শিত জিডিপি বাস্তব অবস্থার চিত্র হতে পারে না। ক্ষমতাসনি সরকার সব সময়ই জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার বাড়িয়ে দেখানোর চেষ্টা করে থাকে। এর প্রমান হচ্ছে প্রতি বছর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো জিডিপি প্রবৃদ্ধির যে পরিসংখ্যান প্রকাশ করে সরকারের দেয়া পরিসংখ্যানে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার তার চেয়ে অন্তত ১ থেকে দেড় শতাংশ বেশি হয়। বছর শেষে কোনো পক্ষই তাদের দেয়া পরিসংখ্যান থেকে সরে আসে না। প্রশ্ন হলো, একটি নির্দিষ্ট বছরে কোনো জনপদের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার দু’রকম হবে কোনো? আরো একটি বিষয় এখানে লক্ষ্য করার মতো তাহচ্ছে যারা অর্থনীতি নিয়ে কাজ করেন না বা অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয় চর্চা করেন না তারা গ্রস ডমেস্টিক প্রোডাক্ট (জিডিপি) এবং গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্টের মধ্যে কি পার্থক্য তা অনুধাবন করতে পারবেন না। কোনো এক বছরে দেশের অভ্যন্তরে যে পণ্য ও সেবা উৎপাদিত হয় তার মোট মূল্যই হচ্ছে গ্রস ডমেস্টিক প্রোডাক্ট বা জিডিপি। আর জিডিপি’র সঙ্গে পণ্য রপ্তানি আয়, রেমিটেন্স, এবং বৈদেশিক আর্থিক সহায়তা যুক্ত হয়ে যে আর্থিক পরিমাণ দাঁড়ায় তা হচ্ছে গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট বা জিএনপি। জিএনপি’র পরিমাণ সব সময়ই জিডিপি’র চেয়ে বেশি হবে।
মাথাপিছু গড় জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে এটা শুনতে বেশ ভালোই লাগে। কিন্তু আমরা অনেকেই জানিনা মাথাপিছু গড় জাতীয় আয় আসলে কি? মাথাপিছু গড় জাতীয় আয় দিয়ে কখনোই একজন নাগরিকের আর্থিক সামর্থ অনুধাবন করা যায় না। বরং মাথাপিছু জাতীয় আয় হিসাব করে সাধারণ মানুষের আয় নিয়ে এক ধরনের পরিহাস করা হয়। নির্দিষ্ট বছরে একটি দেশের জাতীয় আয়কে মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে যে ফিগার পাওয়া যায় সেটাই হচ্ছে মাথাপিছু গড় জাতীয় আয়। মাথাপিছু গড় আয় দিয়ে কখনোই একটি দেশের সব মানুষের আর্থিক সামর্থ এবং পরিস্থিতি বিচার করা যায় না। কারণ দেশে সব মানুষ একই রকম আয় করে না। যেমন, মি. করিম এর বার্ষিক আয় হয়তো ১০ কোটি টাকা। আর মি.খলিলের বার্ষিক আয় হয়তো ২ লাখ টাকা। এক্ষেত্রে তাদের গড় জাতীয় আয় হবে ৫ কোটি ১ লাখ টাকা করে। এই পদ্ধতিতে গড় জাতীয় আয় হিসাব করার ফলে উভয়ের প্রতিই অবিচার করা হচ্ছে। কারণ মি.করিমের আয়কে অর্ধেকে নামিয়ে হিসাব করা হচ্ছে। আর মি. খলিলের আয় সাংঘাতিকভাবে বাড়িয়ে দেখানো হচ্ছে,যা তার প্রকৃত আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সরকার সব সময়ই মাথাপিছু গড় জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করার চেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু তারা একবারও বলছেন না দেশে আয় বৈষম্য কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং সাধারণ মানুষ কতটা আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যে রয়েছে। যারা নিম্ন আয় এবং নির্দিষ্ট অর্থ উপার্জনকারি মানুষ তারা জানেন বাজারে বিদ্যমান অস্বাভাবিক উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে তাদের অবস্থা আজ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। মাঝে মাঝেই পত্রিকার সংবাদ প্রকাশিত হয়, ব্যাংকের আমানত হ্রাস পাচ্ছে। এ জন্য বিভিন্ন কারণকে দায়ী করা হয়। কিন্তু তারা এটা বলছেন না যে, মানুষ সংসারের ব্যয় নির্বাহ করতে ব্যর্থ হচ্ছেন বলে সঞ্চয় করার মতো উদ্বৃত্ত অর্থ যোগার করতে পারছেন না। তারা নতুন করে ব্যাংকে আমানত সংরক্ষণের পরিবর্তে আগে থেকেই ব্যাংকে যাদের আমানত ছিল তা তুলে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করছেন।
অর্থনীতিবিদদের মাঝে একটি কথা বেশ প্রচলিত আছে। বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের সঙ্কটের প্রসঙ্গ এলেই তারা অত্যন্ত বিজ্ঞের মতো বলে থাকেন, একটি দেশের তিন মাসের আমদানি ব্যয় মোটানোর মতো বৈদেশিক মুদ্রা থাকলে তাকে সন্তোষজনক বলা যেতে পারে। কথাটি এমনভাবে বলা হয় যেনো একটি স্বত:সিদ্ধ এবং এর কোনো ব্যত্যয় ঘটার সুযোগ নেই। কিন্তু এটা কোনো অর্থনৈতিক থিউরি নয়। কোনো দেশের এক মাসের আমদানি ব্যয় মেটানোর মতো বৈদেশিক মুদ্রা থাকলেও তাকে সন্তোষজনক বলা যেতে পারে। আবার কোনো দেশের ৫ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানোর মতো বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ থাকলেও তা সন্তোষজনক নাও হতে পারে। যেমন কোনো দেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ কমে গিয়ে একমাসের আমদানি ব্যয় মেটানোর মতো রিজার্ভ থাকলেও তাকে সন্তোষজনক বলা যেতে পারে। যদি দেশটি একমাসের মধ্যেই পর্যাপ্ত পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা যোগানে ব্যবস্থা করতে পারে। আবার ৫ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানোর মতো রিজার্ভ থাকলেও তা আতঙ্কজনক পরিস্থিতির ইঙ্গিত দিতে পারে,যদি দেশটি বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় সাংঘাতিকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং সেই তুলনায় বৈদেশিক মুদ্রা যোগানোর ব্যবস্থা করতে না পারে। অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন, তিন মাসের আমদানি ব্যয় মেটানোর মতো বৈদেশিক মুদ্রা দেশটি সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করতে পারবে। কিন্তৃু বৈদেশিক মুদ্রা যোগানের ব্যবস্থা সরকারের যোগ্যতার উপর নির্ভর করে অনেক খানিই। ভুল পথে যাত্রা শুরু করলে যে কোনো সময় বৈদেশিক মুদ্রার পর্বত প্রমান রিজার্ভ নিয়েও শঙ্কায় ভুগতে হতে পারে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের স্থিতি এক সময় ৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের রেকর্ড পরিমাণে উন্নীত হয়েছিল। এটা ছিল সেই সময় সার্ক দেশগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ। এ নিয়ে আমাদের গর্বের কোনো শেষ ছিল না। তখন কোনো কোনো মহল থেকে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছিল এই বলে যে, রিজার্ভের এই স্ফীতি দীর্ঘ দিন থাকবে না। কিন্তু সেই সময় কোনো সতর্কবাণীতেই কর্ণপাত করা হয়নি। সেই সময় বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার যদি বাজার ভিত্তিক করা হতো তাহলে পরিস্থিতি এতটা খারাপ নাও হতে পারতো। বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়া সত্বেও বিনিময় হার ফিক্সড রাখা হয়। এতে আমদানিকারকগণ কিছু সময় লাভবান হলেও পরবর্তীতে এক সময় বাংলাদেশ ব্যাংক চাহিদা মতো মার্কিন ডলার সরবরাহ করতে না পাবার কারণে কার্ব মার্কেট চাঙ্গা হয়ে উঠে। আমদানিকারকগণ ব্যাংকিং চ্যানেলের বাইরে থেকে তাদের প্রয়োজনীয় মার্র্কিন ডলার উচ্চ মূল্যে যোগার করতে থাকে। পণ্য রপ্তানিকারকগণ স্থানীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটলে বেশি মার্কিন ডলারের বিপরীতে বেশি অর্থ পাবেন এই প্রত্যাশায় রপ্তানি আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বিদেশে রেখে দিচ্ছেন অথবা হুন্ডির মাধ্যমে দেশে নিয়ে আসছেন। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার ফিক্সড করে রাখার কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত রেমিটেন্স খাত। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার বাজারভিত্তিক করা না হলে এবং হুন্ডি ব্যবসায়িদের যদি নিয়ন্ত্রণ করা না যায় তাহলে রেমিটেন্স প্রত্যাশিত মাত্রায় বৃদ্ধি পাবে না। এই খাতে কিছু নগদ আর্থিক প্রণোদনা দিয়ে কোনো কাজ হবে না। বৈধ চ্যানেলের মাধ্যমে রেমিটেন্স প্রেরণ করা হলে প্রতি মার্কিন ডলারের বিপরীতে স্থানীয় মুদ্রায় যদি ১০ থেকে ১৫ টাকা কম পাওয়া যায় তাহলে কেউ কি ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিটেন্স প্রেরণ করতে চাইবে? এ ছাড়া ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিটেন্স প্রেরণের ক্ষেত্রে যে জটিলতা মোকাবেলা করতে হয় হুন্ডির ক্ষেত্রে তা নেই। একজন প্রবাসী শ্রমিক চাইলেই তার কর্মস্থল থেকে সর্ট লিভ নিয়ে ব্যাংকে গিয়ে দেশে রেমিটেন্স প্রেরণ করতে পারবেন না। কিন্তু তিনি যদি হুন্ডির মাধ্যমে রেমিটেন্স দেশে প্রেরণ করেন তাহলে হুন্ডি ব্যবসায়িদের স্থানীয় এজেন্টগণ প্রবাসী শ্রমিকের আবাসিক ভবনে গিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করবেন। এর বিপরীতে দেশে থাকা তাদের এজেন্টগণ স্থানীয় বেনিফিশিয়ারিদের বাসায় গিয়ে রেমিটেন্সকৃত অর্থ পৌঁছে দেবেন। বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশি ব্যাংকগুলো যদি এজেন্টের মাধ্যমে প্রবাসী কর্মীদের বাসায় গিয়ে রেমিটেন্সকৃত অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে পারবেন এবং দেশে আসার পর রেমিটেন্সকৃত অর্থ স্থানীয় বেনিফিশিয়ারিদের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছে দিতে পারতেন তাহলে এই সমস্যা অনেকটাই সমাধান হতে পারতো। রেমিটেন্স প্রোপার চ্যানেলে দেশে আনতে হলে দু’টি কাজ করতে হবে। প্রথমত,বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার বাজার ভিত্তিক করতে হবে অথবা দ্বিতীয়ত, হুন্ডি ব্যবসায়ীদের তৎপরতা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে।
প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় যেসব প্রকল্প গ্রহণ করা হয় তার বিপরীতে বিপুল অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ করা হয়। বছরের প্রথম ৯ মাস বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নের তেমন কোনো অগ্রগতি প্রত্যক্ষ করা যায় না। শেষ তিন মাসে তড়িঘড়ি করে প্রকল্প বাস্তবায়নের নামে অর্থ ব্যয় করা হয়। বছর শেষে দেখানো হয়, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির এত শতাংশ বাস্তবায়িত হয়েছে। এটা আসলে প্রকল্প বাস্তবায়ন নয় আসলে বলা উচিৎ বরাদ্দকৃত অর্থের এত শতাংশ ব্যয় করা সম্ভব হয়েছে। এভাবে অর্থ ব্যয়ের প্রতিযোগিতার কারণে গৃহীত প্রকল্প সঠিক এবং মানসম্পন্নভাবে সম্পন্ন হয় না। কয়েক বছর যেতে না যেতেই প্রকল্পে ফাঁটল ধরে অথবা ভেঙ্গে পড়ে।
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করার সময় প্রাক্কলিত ব্যয় এবং নির্মাণ সময় নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু অধিকাংশ প্রকল্পই নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। এতে প্রকল্প ব্যয় এবং বাস্তবায়নের সময় উভয়ই বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এ জন্য কাউকে জবাবদিহি করতে হয় না। যারা প্রকল্প প্রণয়ন করেন তারা যেহেতু জনগণের ট্যাক্সের মাধ্যমে দেয়া রাষ্ট্রীয় অর্থ হতে বেতন-ভাতা পান তাই তাদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা প্রয়োজন। প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত এবং এতে বর্ধিত অর্থ ব্যয় হলে তার দায়িত্ব প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্তদেরই বহন করতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হলে প্রকল্পের ব্যয় যেমন বেড়ে যায় তেমনি জনগণ প্রত্যাশিত সেবা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়। এটা কোনোভাবেই চলতে দেয়া যায় না।
অর্থনীতিতে ভোক্তার উদ্বৃত্ত নামে একটি থিউরি আছে। থিউরিটি এমন- কোনো একজন ভোক্তা হয়তো বাজারে গেলো প্রতি হালি ডিম ৫০ টাকায় ক্রয় করার জন্য। কিন্তু বাজারে গিয়ে তিনি হয়তো ৩০ টাকা দিয়ে প্রতি হালি ডিম ক্রয় করতে পারলেন। এতে ভোক্তা যে আত্মতৃপ্তি লাভ করবেন এটাই ভোক্তার উদ্বৃত্ত। কিন্তু ভোক্তা ৫০ টাকা প্রতি হালি ডিম ক্রয় করার লক্ষ্য নিয়ে বাজারে গিয়ে যদি ৭০ টাকা দিয়ে এক হাল ডিম ক্রয় করতে হয় তাহলে তিনি যে মানসিক কস্ট পাবেন তাকে আমরা অর্থনীতির পরিভাষায় কি বলবো? এটা কি কনজুমার্স ডেফিসিট বলবো? অর্থনীতিবিদগণ এ ব্যাপারে ভালো বলতে পারবেন। তবে আমাদের এখন ভোক্তার উদ্বৃত্ত তত্ত্ব ভুলে যেতে হবে। এখন আমাদের ভোক্তার মানসিক কষ্ট এবং উদ্বেগ নিয়ে কাজ করতে হবে।
এম এ খালেক: অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ম্যানেজার, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএলসি ও অর্থনীতি বিষয়ক লেখক।